গল্প পড়ার গল্প
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মাটি’
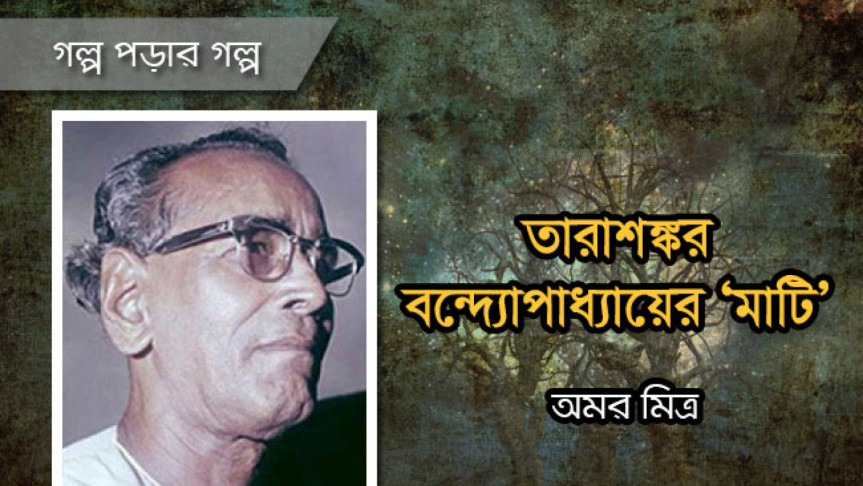
আমার গল্প শোনার আরম্ভ আপনাদের মতো মা-ঠাকুমা, কাকিমা-দিদিদের কাছে। সেই গতখালির ভূতের গল্পে যার শুরু, তা এখনো ভূতুড়ে নেশায় আচ্ছন্ন রেখেছে আমাকে। হ্যঁ, গল্পের টান এমন, সেই ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের তুলোর কারবারির মতো। আমাকে সে টানে। ভালো লাগলে মজে যাই। ক্ষুধিত পাষাণ, মধ্যবর্তিনী থেকে পায়রাকুলি গাঁয়ের বুড়ো পিথা হেমব্রমের কাছে শোনা সাঁওতাল জাতির সৃষ্টি পুরাণ সবই আমার কাছে পরম মুগ্ধতা আনে। সত্যি কথা বলতে কি, গল্প শোনা আর পড়ার চেয়ে সুন্দর অভিজ্ঞতা কী আছে এই জীবনে। তা সে গল্প বাংলা হোক, অন্য ভারতীয় ভাষার হোক, রুশী হোক আর লাতিন আমেরিকান হোক। আমার গল্প পাঠ শুরু সোনার কাঠি-রুপোর কাঠি, রাজকন্যা রাজপুত্তুর আর রাক্ষসে।...তারপর পড়েই চলেছি। আর সেখানেই প্রকৃত পাঠ শুরু রবীন্দ্রনাথ আর আন্তন চেখভে। মনিহারা, শেষের রাত্রি, ক্ষুধিত পাষাণ আর কেরানির মৃত্যু, ছ’নম্বর ওয়ার্ড, গুজবেরি ইত্যাদি আশ্চর্য গল্পে। গল্প পাঠ চলছে।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেছি আমি বাল্যকাল থেকে। রাঢ়ের মানুষ এই লৌকিক দেবতা প্রতিম লেখক আমাদের এলাকায় থাকতেন। আমি দেখেছি বাড়ির সামনে একটি ডেক চেয়ারে তিনি গা এলিয়ে শীতের রোদ পোহাচ্ছেন। আমি তখন ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তকে তাঁর ডাক হরকরা গল্পটি পড়ে বিচিত্র বিস্ময়ে অভিভূত। তারাশঙ্করকে ধীরে ধীরে পড়েছি, পড়তে পড়তে বড় হয়েছি। গল্প আর উপন্যাস, দুয়ে তাঁর সিদ্ধি। যে গল্প তারাশঙ্কর আমাদের সাহিত্যে দিয়ে গেছেন, সেই জলসাঘর, তারিণী মাঝি, ডাইনি, দেবতার ব্যাধি, বরমলাগের মাঠ, অগ্রদানি, নারী ও নাগিনী, কালাপাহাড়, তা রাঢ়ের সীমা ছাড়িয়ে ভারতীয় সাহিত্যের মণিমুক্ত। বিশ্বসাহিত্যে এমন এক লেখক বিরল, এমন তীব্র প্যাশন, এমন নিষ্ঠুরতা, এমন আদিমতা আমাদের সাহিত্যে তারাশঙ্কর ব্যতীত আর কে দিয়েছেন? আমার মনে পড়ে তাঁর প্রয়াণের দিনে সকাল থেকে শোকাহত হয়ে একা একা বসেছিলাম তাঁর বাড়ির সমুখের ঘাস জমিতে।
তারাশঙ্কর আমাদের প্রথম লেখক, যিনি আমাদের চেনালেন জমি আর মাটি। জমির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। তাঁর উপন্যাস আর গল্পে আমরা প্রথম নিম্নবর্গের মানুষের ভূমি ক্ষুধার কথা অনুভব করি। ‘মাটি’ নামের একটি স্বল্প পরিচিত গল্পের কথা আমি বলি। দীর্ঘ এই গল্প দূর পাটনা জেলার কোনো এক জীওনলালের। সে পরে তার গ্রামের মুসহর কন্যা লছমনিয়ার ডাকে মেওয়ালাল হয়ে যায়। গ্রীষ্মের অবসাদগ্রস্ত মধ্য দুপুর, ঝিমিয়ে আছে শহর, উত্তর কলকাতার গলিপথে ডাক ওঠে মাটি চাই—মাটি। গঙ্গার মাটি বেচে বেড়ায় যে লোকটি, সে এক বিচিত্র দর্শন উলঙ্গপ্রায় মানুষ। তার বিবরণ দেন লেখক এইভাবে, তার পরনে শুধু একটা নেংটি, সর্বাঙ্গ কাদায় আবৃত। একজন সুস্থ সহজ মানুষের দেহ এমনভাবে বিকৃত হয়ে যায়! লম্বা একটি মানুষ বোঝা বয়ে খাটো হয়ে যায় এই ভাবে? পা থেকে কোমর পর্যন্ত শরীরের নিচের দিকটা সহজ স্বাভাবিক, সরল সোজা পা, প্রতিটি পেশি সুগঠিত, কিন্তু উপরের দিকটায়—কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত অংশটা বিপুল চাপ দিয়ে কেউ যেন দেহের কাঠামোটা ভেঙেচুরে বিকৃত আর খাটো করে দিয়েছে। মাটি বয়ে বয়ে সে এমন।
তারাশঙ্কর যে গল্প আরম্ভ করেন, সেই গল্প আমার বাল্যস্মৃতিকে ফিরিয়ে আনে। সেই জীবিকা লুপ্ত। সেই মানুষটি তার মহাভারতের মতো গল্প নিয়ে লুপ্ত। চলে গেছে আমার সেই বাল্য-দুপুর। আমি তারাশঙ্করের এই গল্পের ভেতর দিয়ে আরম্ভে ফিরে যাই উত্তর কলকাতার সেই দুপুরে। কিন্তু এই গল্প সেই দুপুরের নয়। এই গল্প এই ভারতবর্ষের। সেই মাটিওয়ালা মেওয়ালাল এই শহরে আসা এক ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষ। তার জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার কাহিনী এই গল্প। আমার কাছে তারাশঙ্করের এই গল্প অতি জরুরি এই কারণে যে সেই অতকাল আগে তিনি মাটি থেকে কৃষকের উচ্ছেদের যে কাহিনী লিখেছিলেন, তা এখনো সত্য। ভয়ানক সত্য।
এই গল্প লেখক লিখেছিলেন যখন, তখন জমিদারি আছে, সায়েবরা আছে। সাতচল্লিশের আগে। মাটিওয়ালা মেওয়ালালের বাবা রতনলাল নিকৃষ্ট জমি বন্দোবস্ত নিয়েছিল জমিদারের কাছ থেকে। বন্দোবস্ত নিয়ে সেই জমি সরস করে তুলেছিল রতনলাল আর সে বুড়ো হলে তার ছেলে জীওনলাল—এই মেওয়ালাল। ফসলে ফসলে সেই জমি বহু প্রসবিনী হয়ে ওঠে। সেখানে মজুরি দিতে আসে লছমনিয়া আর তার বাপ। লছমনিয়ার তিনবার সাগাই হয়েছে, মুসহর কন্যার তিন স্বামীই মরেছে। লছমনিয়া তাই আর ওসবে নেই। জীওনলালের জমিতে খাটে। সেই জমির সঙ্গে সে জড়িয়ে যায়। জড়িয়ে আছে তো তার মেওয়ালাল-জীওনলাল। সে জমিতেই যেন ঘুমোয়, জমির ফসলের দিকে তাকিয়ে তার প্রাণ জুড়োয়। সে এতটাই সেই জমিতে সম্পৃক্ত যে তার বাপ রতনলাল মরে গেলে সে দাহ করে এসে জমিতেই গিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। বাপের মৃত্যুর পর জমিদার তাকে রায়ত হিসেবে মেনে নেয় না।
তারাশঙ্কর এই গল্পে মৌলিক প্রশ্ন তোলেন, মেওয়ালাল বলে, ভগোয়ানের বিধান বাপের স্বভাব পায় ছেলে, চেহারা পায় ছেলে, বাপের রোগ পায় ছেলে, বাপের দেনা শোধ করে ছেলে... কিন্তু বাপের ক্ষেত-খামার ছেলে পায় না কেন? জমিদারের দপ্তরখানায় বাপের জায়গায় ছেলের নাম নথিভুক্ত করাতে জমিদারের বড়ই অনীহা। আসলে এই গল্প জমিদারি উচ্ছেদের আগের গল্প। সেখানে রায়তের ভাগ্য জমিদারের ওপর নির্ভর। জমি থেকে উচ্ছেদ হয় মেওয়ালাল। কৃষকের জীবন নানা ফড়ে দালাল—তহশিলদার, মুন্সির হাতে বিপর্যস্ত হয়। তারপর আসে কত রকম প্রতিরোধের নিষ্ফল প্রয়াস।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জমি মানুষ আর মানুষের আদিমতা নিয়ে বেঁচে থাকার ভয়ংকর প্রয়াস যেমন এঁকেছেন এই গল্পে, তা তিনিই পারতেন। সেই কাহিনী এই দীর্ঘ গল্প। ভীষণ বন্যায় জাহাজঘাটা ভেসে যায়। তারা দুজনে উঠে আশ্রয় নেয় একটি গাছের ওপর। তারা ভেঙেছিল দেয়াল, তারা গুপ্তধনের আশায় তা ভেঙেছিল। তাতেই সব ভাসল। তারপর গ্রেপ্তার, বিচার, জেল। জেল থেকে বেরিয়ে সাক্ষাৎ হয় সাপিন লছমনিয়ার সঙ্গে। সে এক কালো সায়েবের বাংলোয় আয়া। দুটি বাচ্চাকে দেখে। আর সায়েব তার পেটেও একটা বাচ্চা দিয়েছে। সে বাচ্চা দেখে মেওয়ালাল কলকাতায় আসে ভাগ্য অন্বেষণে।
এই গল্প এক গভীর প্রেমের, উচ্ছেদের প্রতিরোধের। চিরকালীন। যে গঙ্গায় তার জমি ভেসে গেল বন্যায়, সে গঙ্গার মাটি বেচে, নিজের মাটি বেচেই যেন তার দিনগুজরান। মাসের প্রথমে ১০ টাকা পাঠায় সে লছমনিয়ার কাছে। কী স্নিগ্ধ হয়ে আসে তখন এই গল্প। হ্যাঁ, মেওয়ালাল বুঝি দেবতাই হয়ে ওঠে বড় লেখকের বড় কলমে।






















 অমর মিত্র
অমর মিত্র


















